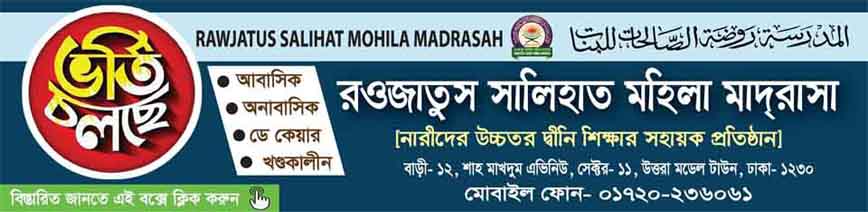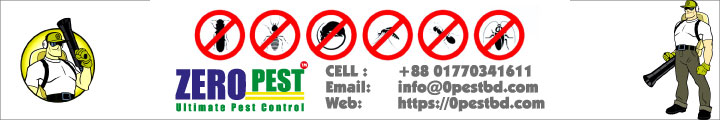ব্রিটেনে সম্প্রতি এক গবেষণার অংশ হিসেবে ২০ হাজারের বেশি করোনার টিকা নেওয়া মানুষকে নজরদারির আওতায় আনা হয়। তাতে দেখা যায়, টিকার দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার দুই সপ্তাহের মধ্যেই প্রায় সবার শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে।
ডেল্টা ধরনের বিরুদ্ধে বর্তমান টিকাগুলো কম কার্যকর বলে উদ্বেগ প্রকাশ করা হলেও বিশ্লেষণে দেখা গেছে, অ্যাস্ট্রাজেনেকা ও ফাইজার-বায়োএনটেক টিকা নিলে রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি করানোর হার ৯২–৯৬ শতাংশ কমে যায়। এছাড়াও, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ঝুঁকিও একেবারেই কম।
তা সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ এখনও টিকা নিতে অনিচ্ছুক। যুক্তরাজ্যের ১০–২০ শতাংশ, জাপানের প্রায় ৫০ শতাংশ এবং ফ্রান্সের প্রায় ৫০ শতাংশ মানুষ টিকা নিতে চায় না।
এর ফলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয়েছে সাংস্কৃতিক যুদ্ধ। অনলাইনে অনেকেই বলে বেড়াচ্ছেন যে যারা টিকা নিতে চান না তারা হয় মূর্খ, নয়তো স্বার্থপর। তবে মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, মানুষের টিকা নিতে অনীহার পেছনে বেশ কিছু জটিল কারণ রয়েছে।
টিকা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নির্ভর করে যে পাঁচটি প্রভাবকের ওপর
টিকা নিতে অনিচ্ছুক সবাই-ই যে টিকাবিরোধী, ব্যাপারটা এমন নয়। টিকায় অনাগ্রহীদের বড় একটা অংশেরই কোনো রাজনৈতিক এজেন্ডা নেই। তারা এমনকি বিজ্ঞানবিরোধীও নন। এই মানুষগুলো আসলে টিকা নেবেন কি নেবেন না, তা নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন।
সুখবর হচ্ছে, প্রথমে যারা টিকা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছিলেন, তাদের অনেকেই মত পাল্টেছেন। সৌভাগ্যক্রমে, ২০১৯-এর ডিসেম্বরে প্রথমবারের মতো সার্স-কোভ-২ ভাইরাস শনাক্ত হওয়ার অনেক আগে থেকেই বিজ্ঞানীরা টিকা নেওয়া নিয়ে কিছু মানুষের দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগার কারণ বের করার জন্য গবেষণা করছিলেন। তাদের মতে, মোটাদাগে পাঁচটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগা মানুষগুলো টিকা নেবে কি না-
বিশ্বাস: টিকার কার্যকারিতা ও নিরাপত্তা, এবং নীতিনির্ধারকদের টিকাপ্রদানের পদ্ধতির ওপর টিকাগ্রহীতার বিশ্বাস।
নিশ্চয়তা: রোগটিকে টিকাগ্রহীতা নিজের স্বাস্থ্যের জন্য গুরুতর ঝুঁকির কারণ মনে করে কি না।
হিসাবনিকাশ: টিকা নেওয়া কতটুকু লাভজনক হবে সেই হিসাবনিকাশ।
সুবিধা: টিকা নেওয়ার প্রক্রিয়া ওই ব্যক্তির জন্য কতটা সুবিধাজনক হবে।
সামষ্টিক দায়িত্ব: নিজে টিকা নিয়ে অন্যদের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করার ইচ্ছা।
এগুলো ছাড়াও আরও কিছু কারণ থাকতে পারে টিকা নেওয়ার অনীহার পেছনে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে প্রায় ১০ শতাংশ মানুষ সূঁচ ভয় পায় বলে টিকা নিতে চায় না।
পক্ষপাত
মানুষের মধ্যে দুটো পরপস্পরবিরোধী প্রবণতা একসঙ্গে কাজ করে—’নেতিবাচক পক্ষপাত’ ও ‘ইতিবাচক পক্ষপাত’। এই প্রবণতা দুটো মানুষের যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করে।
কোনো ঘটনার নিয়ন্ত্রণ যখন আমাদের হাতে থাকে না, তখন নেতিবাচক পক্ষপাত কাজ করে। কোনো নেতিবাচক তথ্য কানে এলেই সেটি আমাদের মনে স্থায়ী আসন গেড়ে বসে। অন্যদিকে আমাদের আত্মবিশ্বাস যখন ভালো থাকে, তখন ইতিবাচক পক্ষপাত বেশি কাজ করে।
এছাড়াও আমাদের মধ্যে আরেক ধরনের পক্ষপাত রয়েছে, যা নিশ্চয়তা খোঁজে। কিছু মানুষ আছে যারা প্রতিনিয়ত তথ্য-উপাত্তের খোঁজে থাকে। তারা নিশ্চিত হতে চায়, যারা টিকা নিয়েছে তাদের কত শতাংশ সুস্থ আছে কিংবা টিকার কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে কি না। এ ধরনের মানুষ টিকা নেওয়ার ক্ষেত্রে বেশি দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগে।
আরও পড়তে পারেন-
- প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের বিবাহ্ সম্পর্কে শরয়ী বিধান
- ইসলামের আলোকে নারীর কর্মপরিধি
- সালাম: উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি রক্ষার অন্যতম বাহন
- বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ: বাস্তবতা ও অপপ্রচার
- সকালের ঘুম যেভাবে জীবনের বরকত নষ্ট করে
অনেকেই আছে, মনে মনে আগে থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখেন যে টিকা নেওয়া বিপজ্জনক। তারা ‘টিকা নেওয়া কি বিপজ্জনক?’ লিখে গুগলে সার্চ দেন। তখন টিকা সম্পর্কে নেতিবাচক খবরগুলোই বেশি চোখে পড়ে তার।
এছাড়াও অনেকেরই, বিশেষ করে দরিদ্রদের মনে হয় তার পক্ষে টিকা পাওয়া কঠিন হবে। এ কারণেও অনেকে টিকা নেওয়া নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগেন।
তাছাড়া নিম্ন আয়ের অনেক মানুষের কাছেই টিকাকেন্দ্রে যাওয়ার খরচ অনেক বেশি মনে হতে পারে। বেকার ও নিম্ন আয়ের অনেক মানুষই এ কারণে টিকা নিতে অনাগ্রহী হয়ে পড়ে।
এ সমস্যা সমাধানে টিকাদান কর্মসূচি একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। গবেষণায় দেখা গেছে, মসজিস, মন্দির, গির্জা, গুরুদুয়ারার মতো উপাসনালয়ে টিকা কার্যক্রম চালিয়ে ভালো ফল পাওয়া গেছে।
টিকাভীতি দূর করার উপায়
সমাধান তাহলে কী?
এ সমস্যার সহজ সমাধান নেই। তবে স্বাস্থ্য-কর্তৃপক্ষ টিকার ব্যাপারে সহজে বোধগম্য ও সঠিক তথ্য প্রচার করতে পারে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এবং টিকার ট্রায়াল ঠিকমতো দেওয়া হয়েছে কি না, এ নিয়েই মানুষের উদ্বেগ বেশি।
প্রথম উদ্বেগ নিরসনের জন্য করোনার তুলনায় টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি যে একেবারেই কম, তা নিয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালানো যেতে পারে। মানুষকে সচেতন করার জন্য তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা যেতে পারে। দ্বিতীয় উদ্বেগ নিরসনের জন্য টিকা উৎপাদনের ইতিহাস মানুষকে বেশি বেশি করে জানাতে হবে। যেমন: মানুষকে জানাতে হবে, এমআরএনএ ভ্যাকসিন কয়েক দশকের গবেষণার ফল। এর কার্যকারিতাও অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত।
গবেষক সারাহ জোন্স বলেছেন, সরকারগুলোর উচিত জনগণের কাছে প্রতিনিয়ত টিকা সম্পর্কে সঠিক তথ্য সরবরাহ করা। সূত্র-বিবিসি।
উম্মাহ২৪ডটকম: এমএ