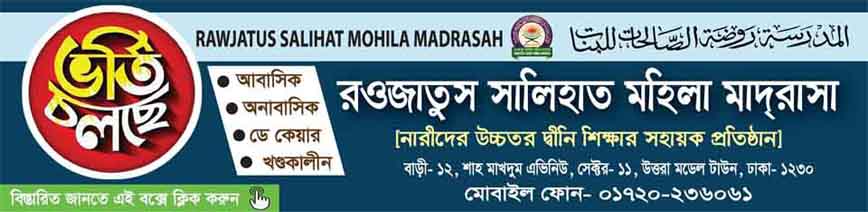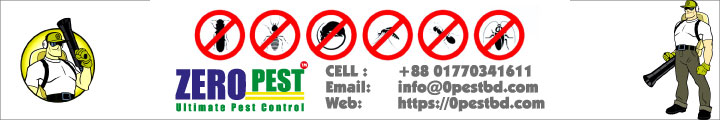ক্লারা ফেরেইরা মার্কুইজ (ব্লুমবার্গ ওপিনিয়ন): রিটুইট করা এক কৌতুক প্রকাশ করায় স্বাধীন একটি ওয়েবসাইটের প্রধান সম্পাদককে কারাদণ্ড দিয়েছে রাশিয়া। এরমধ্য দিয়ে, প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বাক-স্বাধীনতা রুদ্ধ করার অধ্যায়ে আরেকটি অধঃপতন যুক্ত হলো।
গতমাসে বিরোধী নেতা অ্যালেক্সি নাভালনিকে গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড দেওয়ার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয় রাশিয়ায়। তখন নাভালনির বিচারকে পরিহাস করে টুইটারে কৌতুকটি লেখেন এক ব্যবহারকারী। সেটি প্রকাশের অভিযোগে সম্পাদকের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা নেওয়া হলো; তা তুলে ধরছে টুইটার পুতিনের স্বৈরশাসনের জন্য কতবড় হুমকি। শুধু টুইটার নয়, টিকটক ও ইউটিউবের মতো অন্যান্য জনপ্রিয় সামাজিক মাধ্যম হয়ে উঠেছে কর্তৃত্ববাদি, অগণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ক্ষেত্র।
স্মার্টফোন আর সুলভ ইন্টারনেট সংযোগের বদৌলতে দেশে দেশে অনলাইনে নাগরিক মতপ্রকাশের চর্চা বাড়ছে। সেখানে সরকারি দমন-পীড়ন আর দুর্নীতি নিয়ে দু’কথা লিখছেন সাধারণ মানুষ। তবে যেখানে বিরোধীমত সংগঠিত এবং প্রতিরোধের জন্য শক্তিশালী অনলাইন সম্প্রদায় গড়ে উঠছে; সেখানেই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে বিশ্বের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা।
এমনকি খোদ চীনও সে প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। দুই দশক আগে নাগরিক সমাজের অনলাইন গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে চীন তৈরি করে ‘গ্রেট ফায়ারওয়াল’ ব্যবস্থা। তারপরও, সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিবাদকারীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র জোটগুলি নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খাচ্ছে দেশটির কর্তৃপক্ষ।
শুধু রাশিয়া বা চীন নয়, ভারতেও কৃষক আন্দোলনে বৃহৎ ভূমিকা রাখছে সামাজিক মাধ্যম। পপস্টার রিহানা থেকে শুরু করে পরিবেশবাদী গ্রেটা থুনবার্গও সামাজিক মাধ্যমে এরপ্রতি সমর্থন জানান। প্রতিক্রিয়ায় কৃষকদের দাবিদাওয়া নিয়ে সোচ্চার অধিকার কর্মীদের টুইটার অ্যাকাউন্ট বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয় নরেন্দ্র মোদি সরকার। এমনকি বিরোধীমতের অনেকের ‘ওয়েব এক্সেস’ সীমিত করা হয়েছে। মিয়ানমারের জেনারেলরাও ক্ষমতা দখলের সঙ্গে সঙ্গে অস্থায়ীভাবে ফেসবুক নিষিদ্ধ করে। তারপর, সম্পূর্ণ ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।
সামাজিক মাধ্যম এবং ম্যাসেজ সার্ভিস; বিশেষত যেগুলো ব্যবহারকারীদের গোপনীয়তার স্বার্থে উভয় প্রান্তে ইনক্রিপশন প্রযুক্তি ব্যবহার করে; তারা বিগত কয়েক বছরে দেশে দেশে সরকার বিরোধী আন্দোলন আয়োজনের উপযুক্ত ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। এশিয়ার হংকং থেকে দক্ষিণ আমেরিকার চিলিতে নেতৃত্বহীন বিক্ষোভ অথবা থাইল্যান্ড ও বেলারুশে ছাত্র আন্দোলন; কোনোটাই শুধুমাত্র সাধারণ যোগাযোগের মাধ্যমে সংগঠিত হয়নি। জাতীয় সীমানার গণ্ডি পেড়িয়ে অন্যদেশের আন্দোলনকারীদের অভিজ্ঞতা থেকেও শিক্ষা নেওয়ার সুযোগ তৈরি হয় সামাজিক মাধ্যমের কল্যাণে। এশিয়ার মিল্ক টি অ্যালায়েন্স’ এমন অনুপ্রেরণায় গড়ে ওঠা প্রতিবাদের যথার্থ উদাহরণ। মিয়ানমারের বিক্ষোভকারীরা প্রতিবেশী থাইল্যান্ডের হাঙ্গার গেমস সেল্যুট’সহ অন্যান্য আঞ্চলিক আন্দোলনকে অনুসরণ করছেন।
বিশ্বব্যাপী সচেতন মানুষের এই যে সংযোগ, সেটাই স্বৈরশাসকদের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি।
রাশিয়ায় বিরোধী নেতা নাভালনি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত টেলিভিশনে তার বক্তব্য প্রচার করা হবে না জেনে; ইউটিউবের মাধ্যমে তার দুর্নীতি বিরোধী প্রচারণা চালান। এতে তিনি ব্যাপক সফলতাও পান। তার ভূমিকাকে তুচ্ছ করতে রুশ কর্মকর্তারা নাভালনিকে সামান্য একজন ‘ব্লগার’ বললেও, সেটি আসলে মিথ্যা দাবি। তিনি অনলাইনে মানুষের মনোযোগ তীব্রভাবেই আকর্ষণ করেছেন। বিশেষ করে, পুতিনের বিলাসবহুল ব্যক্তিগত প্রাসাদ নিয়ে তৈরি তার ভিডিওটি ১০ কোটি বার দেখা হয়েছে। ক্রেমলিন বারবার এটি মিথ্যে দাবি করলেও, জনসাধারণের সিংহভাগ তাতে কান দেয়নি। এরপর, গতমাসে আদালতে দেওয়া নাভালনির বক্তব্যের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। সবমিলিয়ে বেশ চাপের মুখেই পড়েছে ক্রেমলিন।
আরও পড়তে পারেন-
- ঋণ বা ধারকর্য পরিশোধে ইসলামের বিধান
- ইতিহাসে আল্লামা আহমদ শফী
- মেধাবী, আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান শিক্ষক ছাড়া শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্ভব নয়
- ইগো প্রবলেম নিয়ে যত কথা
- সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখতে ইসলামের নির্দেশনা
দীর্ঘদিন ধরে বেইজিং- এর চাইতে বেশি অনলাইন স্বাধীনতা দিয়ে এসেছে মস্কো। সেই তুলনায় বেইজিং সামান্যতম বিরোধী মত-প্রকাশের দায়ে দমন করেছে গণমাধ্যম কর্মী; বিশেষ করে অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের। এবার রাশিয়াও সেপথ বেছে নিলো। রুশ কর্তৃপক্ষ চাইছেন, প্রতিবাদের টুঁটি আরও শক্ত করে চেপে ধরতে। জার্মানি থেকে চিকিৎসা নিয়ে ফেরার পর নাভালনির প্রতি জনসমর্থন তাদের স্বাভাবিক কারণেই উদ্বিগ্ন করেছে। ইতোপূর্বে, তাকে নার্ভ এজেন্ট প্রয়োগে হত্যাচেষ্টা করেছিল রুশ গোয়েন্দা সংস্থা- এমন অভিযোগও রয়েছে।
মস্কোর তৎপরতা তাই চোখে পড়ার মতো। সামাজিক গণমাধ্যমগুলিকে নাভালনির পোষ্ট ও ভিডিও সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে ক্রেমলিন। নির্দেশ না মানলে বৈশ্বিক ইন্টারনেট সংযোগ থেকে রাশিয়াকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করার হুমকিও দেওয়া হয়।
বলাবাহুল্য, এই হুমকি বাস্তবে রূপ নিলে- তা হবে সামাজিক মাধ্যমগুলোর জন্যে বিপুল আর্থিক ক্ষতির কারণ। রাশিয়া নিজেও অর্থনৈতিকভাবে লোকসানে পড়বে, তবে আপাতত ক্রেমলিন সেই ঝুঁকি নিতে চায়।
রাশিয়ার অর্থনৈতিক ক্ষতির একটি আভাস দিতে পারে তুলনামূলক ছোট প্রতিবেশী বেলারুশ। দেশটিতে গত নির্বাচন পরবর্তীকালে বিক্ষোভ ঠেকাতে ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। ২১৮ ঘণ্টার এই নিষেধাজ্ঞায় অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় ৩৩৬ মিলিয়ন ডলার। তবে এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব আরও বেশি বলেই ইঙ্গিত মেলে।
গত এক দশক ধরে আন্দোলন সংগঠনের নতুন মাধ্যমে রূপ নেয় সোস্যাল মিডিয়া। ‘আরব বসন্ত’ সংগঠনে প্রথম এর ব্যাপক ব্যবহার চোখে পড়ে। অবশ্য, সেই ভূমিকা বেশ বিতর্কিত।
আরব বসন্তের প্রথম স্ফুলিঙ্গ ছড়ানোর পরের দশকে আজ সামাজিক মাধ্যম হয়ে উঠেছে নানাবিধ অধিকার ও মতচর্চার অঙ্গন। এর কলেবর ও ভুমিকাও বেড়েছ বহুগুণ। সংবাদ প্রচার থেকে শুরু করে, কারো জরুরি চিকিৎসার জন্যে অর্থ সংগ্রহ; নানান কাজে হচ্ছে সফল ব্যবহার। অন্য যেকোনো সময়ের চাইতে বর্তমানেই অনলাইনে সামাজিক মাধ্যমে বেশি সময় কাটাচ্ছেন সকলে।
অবশ্য, অনলাইনে মতচর্চার সকল উদ্যোগ গণতান্ত্রিক শক্তি- সে দাবি করার উপায় নেই। অপসংবাদ ও মিথ্যে প্রচারণার উর্বর ক্ষেত্র হয়ে তা দাবানলের মতো ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, এর সাহায্যেই। মিয়ানমার ও ভারতে নিকট অতীতে মিথ্যে প্রচারণার মাধ্যমে জাতিগত সহিংসতা, দাঙ্গা উস্কে দেওয়ার ঘটনা লক্ষ্য করা গেছে। রোহিঙ্গা গণহত্যারকালে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়াতে নিন্দনীয় ভূমিকা রাখে ফেসবুক। ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট রড্রিগো দুতার্তে তার সমালোচকদের বিরুদ্ধে ফেসবুককে ‘অস্ত্র’ হিসেবে ব্যবহার করছেন। যুক্তরাষ্ট্রে ষড়যন্ত্র তত্ত্ব ছড়িয়ে সমর্থকদের উস্কানি দিয়েছিলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এসব ঘটনা জোরদার করেছে সামাজিক গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণের পক্ষের মত। বিশেষ করে, এসব ক্ষেত্রকে পর্যবেক্ষন এবং যথাযথ নীতির আওতায় পরিচালনার দাবি উঠছে।
তাই গণতন্ত্রপন্থীরা যখন তাদের মতাদর্শ টুইটার বা ইউটিউবে তুলে ধরছেন; তখন চীন ও রাশিয়ার মতো দেশে আগ্রাসী রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যম তাদের বিদেশি সমর্থনপুষ্ট অশুভ শক্তি বলে প্রচারণা চালাচ্ছে।
কোনো আন্দোলন শুধু সামাজিক মাধ্যমের কারণে হয় না। এটাও সত্যি, শুধু অনলাইন সমালোচনা অগণতান্ত্রিক সরকার পতন করতেও পারে না। তারপরও, স্বীকার করতেই হবে, সামাজিক মাধ্যম কর্তৃত্ববাদি শাসনের ভিত্তি অস্থিতিশীল করার মতো শক্তি অর্জন করেছে।
– ক্লারা ফেরেইরা মার্কুইজ, পণ্যবাজার, পরিবেশ, সামাজিক ইস্যু ও সরকারি নীতি নিয়ে ব্লুমবার্গে মতামত কলাম লেখেন ক্লারা ফেরেইরা মার্কুইজ। ইতোপূর্বে, তিনি বার্তা সংস্থা রয়টার্সের ব্রেকিংভিউজ শাখায় সহ-সম্পাদকের পদে ছিলেন। সংস্থাটির সম্পাদক ও প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন; সিঙ্গাপুর, ভারত, ইতালি, যুক্তরাজ্য ও রাশিয়াতে।
উম্মাহ২৪ডটকম: এসএএ